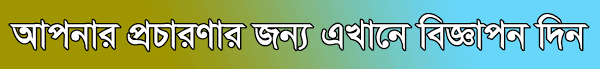তরজমা ও তাফসীর

পরম করুণাময় মেহেরবানী আল্লাহর নামে
﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ﴾
১। আসমানে যা আছে এবং যমীনে যা আছে তার সবই আল্লাহর তাসবীহ করছে। তিনি বাদশাহ, অতি পবিত্র এবং মহা পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।১
১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা আল হাদীদের ১ ও ২ নং টীকা, আল হাশরের ৩৬, ৩৭ ও ৪১ টীকা। পরবর্তী বিষয়ের সাথে এই প্রারম্ভিক কথাটির গভীর সম্পর্কে বিদ্যমান। আরবের ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ সা. এর ব্যক্তিসত্তা, গুণাবলী ও কার্যকলাপে রিসালাতের স্পষ্ট নিদর্শন চাক্ষুষ দেখা সত্ত্বেও এবং হযরত মূসা আ. তাঁর সম্পর্কে তাওরাতে স্পষ্ট ভাষায় যে সুসংবাদ দিয়েছিলেন তা যে তাঁর ছাড়া আর কারো জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না তা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও শুধু এজন্য তাঁকে অস্বীকার করেছিল যে, নিজ জাতি ও বংশের বাইরের আর করো রিসালাত মেনে নেয়া তাদের কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার ছিল। তারা পরিষ্কার বলতো, আমাদের কাছে যা কিছু এসেছে আমরা কেবল তাই মানবো। কোনো অইসরাঈলী নবীর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকেও কোনো শিক্ষা এসে থাকলে তো মেনে নিতে তারা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। এই আচরণের কারণে পরবর্তী আয়াত গুলোতে তাদেরকে তিরষ্কার করা হচ্ছে। তাই এই প্রারম্ভিক আয়াতাংশ দিয়ে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে। এতে প্রথম যে কথাটি বলা হয়েছে তাহলো, বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি বন্তু আল্লাহর তাসবীহ করছে। অর্থাৎ গোটা বিশ্ব-জাহান একথার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যেসব অপূর্ণতা ও দুর্বলতার ভিত্তিতে ইহুদীরা তাদের বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা কায়েম ও বদ্ধমূল করে রেখেছে আল্লাহ তাআ’লা তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি কারো আত্মীয় নন। তাঁর কাছে পক্ষপাতিত্বমূলক (Favouritism) কোন কাজ নেই। তিনি নিজের সমন্ত সৃষ্টির সাথে সমানভাবে ইনসাফ, রহমত ও প্রতিপালক সুলভ আচরণ করেন। কোনো বিশেষ বংশধারা বা কওম তাঁর প্রিয় নয় যে, তারা যাই করুক না কেন সর্বাবস্থায় তাঁর অনুগ্রহ তার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে এবং অন্য কোনো জাতি গোষ্ঠী বা কওমের সাথে তাঁর কোন শত্রুতা নেই যে, তাদের মধ্যে সদগুণাবলী থাকা সত্ত্বেও তাঁর দান ও করুণা থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। এরপর বলা হয়েছে তিনি বাদশাহ। অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের কোন শক্তিই তার ক্ষমতা ও ইখতিয়ারকে সীমিত করতে পারে না। তোমরা তাঁর দাস এবং প্রজা। তোমাদের হিদায়াতের জন্য তিনি কাকে পয়গাম্বর বানাবেন আর কাকে বানাবেন না, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মত পদমর্যাদা তোমরা কবে থেকে লাভ করছে? তারপর বলা হয়েছে, তিনিقدوس মহা পবিত্র। অর্থাৎ তাঁর সিদ্ধান্তে ভুল-ত্রুটির কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে না। তিনি ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র, তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। তোমাদের বুঝ ও উপলব্ধিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পারে, কিন্তু তার সিদ্ধান্তে ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পারে না। শেষ দিকে আল্লাহ তাআ’লার আরো দু’টি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে একটি হলো, তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশারী। অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে কেউ জয়লাভ করতে পারে না। অপরটি হলো তিনি জ্ঞানময়, অর্থাৎ যা কিছু করেন, বুদ্ধি, বিবেক ও প্রজ্ঞার দাবীও হুবহু তাই। আর তাঁর কৌশল ও ব্যবস্থাপনা এতই সুদৃঢ় হয়ে থাকে যে, বিশ্ব-জাহানের কেউই তা ব্যর্থ করতে পারে না।
﴿هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًۭا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ﴾
২। তিনিই মহান সত্তা যিনি উম্মীদের২ মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন যে তাদেরকে তাঁর আয়াত শুনায়, তাদের জীবনকে সজ্জিত ও সুন্দর করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়।৩ অথচ ইতিপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।৪
২. এখানে ‘উম্মী’ শব্দটি ইহুদীদের পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম বিদ্রূপ বা তিরষ্কার প্রচ্ছন্ন আছে। অর্থাৎ ইহুদীরা যাদেরকে অবজ্ঞা করে ‘উম্মী’ বলে থাকে এবং নিজেদের তুলনায় নগণ্য ও নীচু বলে মনে করে পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময় আল্লাহ তাদের মধ্যেই একজন রাসূল সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজে রাসূল হয়ে বসেননি, বরং তাঁকে পাঠিয়েছেন তিনিই যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের বাদশাহ, মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। তাঁর শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে এরা নিজেদেরই ক্ষতি করবে তাঁর কোনো ক্ষতি করতে এরা আদৌ সক্ষম নয়।
জেনে রাখা দরকার যে, কুরআন মজীদে, ‘উম্মী’ শব্দটি বেশ কটি স্থানে এসেছে। তবে সব জায়গায় শব্দটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং বিভিন্ন জায়গায় আলাদা আলাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও যাদের কাছে অনুসরণ করার জন্য কোন আসমানী কিতাব নেই আহলে কিতাবেরদের বিপরীতে তাদেরকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছেঃ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ আহলে কিতাব ও উম্মীদের জিজ্ঞেস করঃ তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করেছ?” (আলে ইমরানঃ ২০)
এখানে উম্মী বলতে আরবের মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে এবং তাদেরকে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টানদের থেকে স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
কোথাও এ শব্দটি আহলে কিতাবদেরই নিরক্ষর ও আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে অজ্ঞ ও অনবহিত লোকদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছেঃ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ “এই ইহুদীদের কিছু লোক আছে ‘উম্মী’ কিতাবের কোন জ্ঞান তাদের নেই। তারা কেবল নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনাকেই চিনে।” (আল বাকারাহঃ ৭৮)
আবার কোথাও এ শব্দটি নিরেট ইহুদী পরিভাষা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে ‘উম্মী’ বলতে অ-ইহুদী সবাইকে বুঝানো হয়েছে।
যেমন, বলা হয়েছেঃ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ “তাদের মধ্যে এ অসাধুতা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হলো, তারা বলেঃ ‘উম্মীদের অর্থ-সম্পদ লুটেপুটে ও মেরে খাওয়ার কোন দোষ নেই।” (আলে ইমরানঃ ৭৫)
আলোচ্য আয়াতে এই তৃতীয় অর্থটিই গ্রহণ করা হয়েছে। এ শব্দটি ইব্রিয় ভাষায় ‘গোয়েম’ শব্দের সমার্থক। ইংরেজী বাইবেলে এর অনুবাদ করা হয়েছে Gentiles এবং এর দ্বারা সমস্ত অ-ইহুদী বা-ইসরাঈলী লোককে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু শুধু এতটুকু ব্যাখ্যার, সাহায্য এ ইহুদী পরিভাষাটির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা সম্ভব নয়। ইবরানী বা ইব্রিয় ভাষায় ‘গোয়েম’ শব্দটি প্রথমত কেবল জাতি বা কওমসমূহ অর্থে বলা হতো। কিন্তু ক্রমান্বয়ে ইহুদীরা এটিকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে শুরু করে। প্রথমে তারা এটিকে নিজেদের ছাড়া অন্যসব কওমের জন্য নির্দিষ্ট করে। পরে এ শব্দটির অর্থে এ ভাবধারাও সৃষ্টি করে যে, ইহুদীরা ছাড়া অন্য সব জাতিই অসভ্য ও অভদ্র, ধর্মের দিক থেকে নিকৃষ্ট, অপবিত্র এবং নীচ ও হীন। শেষ পর্যন্ত অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা-বিদ্ধেষ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ শব্দটি উদ্দেশ্যে অগ্রীকদের জন্য গ্রীকদের ব্যবহৃত পরিভাষা Barbarian শব্দটিকেও ছাড়িয়ে যায়। রিব্বীদের সাহিত্যে ‘গোয়েম’রা এমনই ঘৃণ্য মানুষ যে, তাদেরকে মানুষ হিসেবে ভাই বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না এবং তাদের সাথে সফরও করা যেতে পারেনা। বরং তাদের কেউ যদি পানিতে ডুবে মারতে থাকে তাহলে তাকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টাও করা যেতে পারে না। ইহুদীরা বিশ্বাস করতো, মাসীহ এসে সমস্ত গোয়েমকে ধ্বংস করে জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলবেন। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আলে ইমরানঃ টীকা ৬৪)
৩. কুরআন মজীদের চারটি স্থানে রাসূলুল্লাহ সা. এর এ বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রত্যেক স্থানই বর্ণনা করার ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। সূরা আল বাকারাহ-এর ১২৯ আয়াতে এসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছ আরববাসীদের একথা বলার জন্য যে, নবী সা. এর নবী হয়েছে আসাকে তারা যে নিজেদের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত বলে মনে করছে, তা ঠিক নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে তা তাদের জন্য একটি বড় নিয়ামত। এটি লাভের জন্য হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল আ. তাদের সন্তানদের জন্য দোয়া করতেন। সূরা আল বাকারাহ-এর ১৫১ আয়াতে এসব গুণাবলী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানরা যেন নবীর সা. মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে এবং আল্লাহ তাআ’লা তাঁকে নবী বানানোর মাধ্যমে যে নিয়ামত তাদের দিয়েছেন তা থেকে পুরোপুরি উপকৃত হতে পারে। সূরা আলে ইমরানের ১৬৪ আয়াতে আবার এসব গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের মানুষগুলোকে একথা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআ’লা তাদের কাছে তাঁর রাসূল পাঠিয়ে কত বড় ইহসান করেছেন। কিন্তু তারা এমনই অপদার্থ যে, তাঁকে কোনো মর্যাদাই দিচ্ছে না। চতুর্থবারের মত এ সূরাতে ঐসব গুণাবলী পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ইহুদীদের একথা জানিয়ে দেয়া যে, মুহাম্মাদ সা. তোমাদের চোখের সামনে যেসব কাজ করেছেন, তা স্পষ্টত একজন রাসূলের কাজ। তিনি আল্লাহর আয়াত শুনাচ্ছেন। এসব আয়াতের ভাষা, বিষয়বস্তু, বর্ণনাভঙ্গি সবকিছুই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তা প্রকৃতই আল্লাহর আয়াত। তা মানুষের জীবনকে সুন্দর, পরিপাটি ও সুবিন্যস্ত করছে, তাদের নৈতিক চরিত্র, অভ্যাস ও রীতিনীতি এবং লেনদেন ও জীবনচারণকে সব রকমের কলূষ-কালিমা থেকে পবিত্র করছে এবং উন্নতমানের নৈতিক মর্যাদায় ভূষিত করছে। এটা ঠিক সেই কাজ যা ইতিপূর্বে সমস্ত নবী-রাসূলও করেছেন। তাছাড়া তিনি শুধু আয়াত সমূহ শুনানোকেই যথেষ্ট মনে করেন না, বরং সবসময় নিজের কথা ও কাজ দ্বারা নিজের বাস্তব জীবনের উদাহরণ দ্বারা মানুষকে আল্লাহর কিতাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝাচ্ছেন। তিনি তাদের এমন যুক্তি, বুদ্ধি ও জ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছেন যা কেবল নবী-রাসূলগণ ছাড়া আর কেউ-ই শিক্ষা দেয়নি। এ ধরনের চরিত্র ও কাজ নবী-রাসূলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুণ। এর সাহায্যেই তাদের চেনা যায়। সত্যিকার অর্থে নিজের কর্মকাণ্ড থেকে যার রাসূল হওয়া প্রমাণিত হচ্ছে তাঁকে তোমরা কেবল এজন্য অস্বীকার করছো, যে তাঁকে তোমাদের কওমের মধ্য থেকে না পাঠিয়ে এমন এক কওমের মধ্য থেকে পাঠানো হয়েছে যাদেরকে তোমরা ‘উম্মী’ বলে অবজ্ঞা করে থাকেন।
৪. এটা রাসূল সা. এর রিসালাতের আরো একটি প্রাণ। ইহুদীদের সত্যোপলদ্ধির জন্য এ প্রমাণটি পেশ করা হয়েছে। তারা শত শত বছর পূর্বে থেকে আরব ভূমিতে বসবাস করে আসছিল। আরবের অজানা ছিল না। তাদের পূর্বতন এ অবস্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলা হচ্ছে, মুহাম্মাদ সা. এর নেতৃত্বে এ জাতির চেহারা যেভাবে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে তা তোমরা নিজ চোখে দেখেছ। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এমন লোক যে অবস্থার মধ্যে ডুবে ছিল তা তোমাদের জানা আছে। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের অবস্থা কি হয়েছে তাও তোমরা নিজ চোখে দেখছ। আর এ জাতির যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের অবস্থাও কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। একজন অন্ধও এই স্পষ্ট পার্থক্য দেখতে ও বুঝতে পারে। এটা কি তোমাদেরকে একথা বিশ্বাস করানোর জন্য যথেষ্ট নয় যে, একজন নবী ছাড়া এটা আর কারো কীর্তি হতে পারে না? বরং এর তুলনায় পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের কীর্তিও ম্লান হয়ে গিয়েছে।
﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا۟ بِهِمْ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾
৩। (এ রাসূলের আগমন) তাদের অন্য লোকদের জন্যও যারা এখনো তাদের সাথে যোগ দেয়নি।৫ আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।৬
৫. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা. এর রিসালাত শুধু আরব জাতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। তা সারা দুনিয়ার সেইসব জাতি ও বংশ-গোষ্ঠীর জন্য যারা এখনো ঈমানদারদের মধ্যে শামিল হয়নি, বরং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে। মূল আয়াতাংশ হলোঃ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ তাদের মধ্য থেকে আরো কিছু লোক যারা এখনো তাদের সাথে শামিল হয়নি। এ আয়াতের مِنْهُمْ (তাদের মধ্য থেকে) শব্দটির দু’টি অর্থ হতে পারে। একঃ সেই অন্যান্য লোকগুলো উম্মীদের মধ্যে থেকে অর্থাৎ তারা হবে দুনিয়ার অ-ইসরাঈলী জাতি –গোষ্ঠীর লোক।
দুইঃ তারা হবে মুহাম্মাদ সা.কে অনুসরণকারী। তবে এখনো ঈমানদারদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, কিন্তু পরে এসে শামিল হবে। এভাবে এ আয়াতটিও সেই সব আয়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. এর রিসালাত সমগ্র মানব জাতির জন্য এবং চিরদিনের জন্য। কুরআন মজীদের আর যেসব স্থানে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে সূরা আল আনআ’মঃ আয়াত ১৯, আল আ’রাফঃ১৫৮, আল আম্বিয়াঃ ১০৭, আল ফুরকানঃ ১, সাবাঃ ২৮; (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবাঃ টীকা ৪৭)
৬. অর্থাৎ এটি তাঁর শক্তি-সমর্থ ও জ্ঞানের বিস্ময়কর দিক যে, তিনি এ ধরনের এক অশিষ্ট উম্মী কওমের মধ্য থেকে এমন মহান নবী সৃষ্টি করেছেন যার শিক্ষা ও হিদায়াত এতটা বিপ্লবাত্মাক ও এমন বিশ্বজনীন স্থায়ী নীতিমালার ধারক, যার ওপর ভিত্তি করে গোটা মানব জাতি একটি মাত্র জাতিতে পরিণত হতে পারে এবং এ নীতিমালা থেকে চিরদিন দিকনির্দেশনা লাভ করতে পারে। যত চেষ্টাই করা হোক না কেন কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে কোনো মানুষই এই স্থান ও মর্যাদা লাভ করতে পারতো না। আরবদের মত পশ্চাদপদ জাতি তো দূরের কথা, দুনিয়ার কোন বড় জাতির সর্বাধিক মেধা-সম্পন্ন ব্যক্তিও এভাবে কোন জাতির চেহারা পুরোপুরি পাল্টে দিতে এবং গোটা মানব জাতিকে চিরদিনের জন্য একটি আদর্শ এবং একটি সংস্কৃতির বিশ্বজনীন ও সর্বাত্মক আদর্শ পরিচালনার যোগ্য হওয়ার মত একটা ব্যাপক নীতিমালা গোটা বিশ্বকে উপহার দিতে পারতো না। এটি আল্লাহর কুদরাতে সংঘটিত একটি মু’জিযা। আল্লাহ তাঁর কৌশল অনুসারে যে ব্যক্তি, যে দেশ এবং যে জাতিকে চেয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে বাছাই করে নিয়েছেন। এতে কোন নির্বোধ যদি মনে কষ্ট পায় তাহলে পেতে থাকুক।
﴿ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ﴾
৪। এটা তাঁর মেহেরবানী, তিনি যাকে চান তা দান করেন। আল্লাহ মহাকরুণার অধিকারী।
﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًۢا ۚ بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ﴾
৫। যাদেরকে তাওরাতের বাহক বানানো হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বহন করেনি৭ তাদের উপমা সেই সব গাধা৮ যা বই-পুস্তক বহন করে। এর চেয়েও নিকৃষ্ট উপমা সেই সব লোকরে যারা আল্লাহর আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলেছে।৯ আল্লাহ এ রকম জালেমদের হিদায়াত দান করেন না।
৭. এ আয়াতাংশের দু’টি অর্থ। একটি সাধারণ অর্থ এবং অপরটি বিশেষ অর্থ। সাধারণ অর্থ হলো, যাদের ওপর তাওরাতের জ্ঞান অর্জন, তদনুযায়ী আমল এবং তাওরাত অনুসারে দুনিয়াকে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তারা তাদের এ দায়িত্ব বুঝেনি এবং তার হকও আদায় করেনি। বিশেষ অর্থ হলো, তাওরাতের ধারক ও বাহক গোষ্ঠী হওয়ার কারণে যাদের কাজ ছিল সবার আগে অগ্রসর হয়ে সেই রাসূলকে সাহায্য-সহযোগিতা করা যার আগমনের সুসংবাদ তাওরাতের স্পষ্ট ভাষায় দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারাই তাঁর সবচেয়ে বেশী শত্রুতা ও বিরোধিতা করেছে এবং তাওরাতের শিক্ষার দাবী পূরণ করেনি।
৮. অর্থাৎ গাধার পিঠে বই-পুস্তকের বোঝা চাপানো থাকলেও পিঠের ওপর কি আছে সে যেমন তা জানে না। অনুরূপ এই তাওরাতের বোঝাও তাদের ওপর চাপানো আছে। কিন্তু তারা আদৌ জানে না, এই মহান গ্রন্থ কি জন্য এসেছে এবং তাদের কাছে কি দাবী করছে।
৯. অর্থাৎ তাদের অবস্থা গাধার চেয়েও নিকৃষ্টত। গাধার কোন বিবেক-বুদ্ধি ও উপলব্ধি নেই বলে সে অক্ষম, কিন্তু এদের তো বিবেক-বুদ্ধি ও উপলব্ধি আছে। এরা নিজেরা তাওরাত পড়ে এবং অন্যদের পড়ায় তাই এর অর্থ তাদের অজানা নয়। এরপরও তারা জেনে শুনে এর হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ও উপেক্ষা করছে এবং সেই নবীকে মানতে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করছে যিনি তাওরাত অনুসারে অবিসংবাদিতভাবে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এরা জানে না বা বুঝে না বলে দোষী নয়, বরং জেনে শুনে আল্লাহর আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলার অপরাধে অপরাধী।
﴿قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا۟ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ﴾
৬। তুমি বল, হে ইহুদী হয়ে যাওয়া লোকগণ!১০ তোমরা যদি ভেবে থাকো যে, অন্য সব মানুষ বাদ দিয়ে কেবল তোমরাই আল্লাহর প্রিয়পাত্র,১১ আর তোমাদের এ ধারণার ক্ষেত্রে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো,১২
১০. এ বিষয়টি লক্ষণীয় যে, এখানে, “হে ইহুদীরা” বলা হয়নি। বলা হয়েছে “হে ইহুদী হয়ে যাওয়ার লোকগণ” অথবা “যারা ইহুদীবাদ গ্রহণ করেছো।” এর কারণ হলো, মূসা আ. এবং তাঁর আগের ও পরের নবী-রাসূগগণ আসল যে দ্বীন এনেছিলেন, তা ছিল ইসলাম। এসব-রাসূলদের কেউই ইহুদী ছিলেন না এবং তাদের সময়ে ইহুদীদের সৃষ্টিও হয়েছিল না। এই নামে এ ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে বহু পরে। ইয়া’কুব আ. এর চতুর্থ পুত্র ইয়াহুদার বংশোদ্ভুত গোত্রটির নামানুসারে এ ধর্মের নামকরণ হয়েছে। হযরত সুলায়মান আ. এর পরে তার সাম্রাজ্যে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলে এই গোত্রটি ইয়াহুদীয়া নামক রাষ্ট্রটির মালিক হয় এবং বনী ইসরাঈলদের অন্যান্য গোত্রগুলো নিজেদের একটি আলাদা রাষ্ট্র কায়েম, করে যা সামেরিয়া নামে খ্যাত হয়। পরবর্তীকালে আসিরীয়রা সামেরিয়াকে শুধু ধ্বংসই করেনি, বরং এই রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠাতা ইসরাঈলী গোত্রগুলোর নাম-নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দিয়েছে। এরপরে শুধু ইয়াহুদা এবং তার সাথে বিন ইয়ামীনের বংশ অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু তার ওপর ইয়াহুদা বংশের প্রভাব ও আধিপত্যের কারণে তাদের জন্য ইয়াহুদ শব্দটির প্রয়োগ হতে থাকে। ইহুদী ধর্মযাজক, রিব্বী এবং আহবাররা নিজেদের ধ্যান-ধারণা, মতবাদ ও ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ অনুযায়ী এই বংশের মধ্যে আকীদা-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় বিধি-বিধানের যে কাঠামো শত শথ বছর ধরে নির্মাণ করেছে তার নাম ইহুদীবাদ। খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে এই কাঠামো নির্মাণ শুরু হয় এবং খৃস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত চলতে থাকে। আল্লাহর রাসূলদের আনীত আল্লাহর হিদায়াতের উপাদান খুব সামান্যই এতে আছে এবং যা আছে তার চেহারাও অনেকখানি বিকৃত হয়েছে। এ কারণে কুরআন মজীদের অধিকাংশ স্থানে তাদেরকে الَّذِينَ هَادُوا বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ সেই সব লোক যারা ইহুদী হয়ে গিয়েছে বা ইহুদীবাদ গ্রহণ করেছে। তাদের মধ্যকার সবাই আবার ইসরাঈলী ছিল না। যেসব অইসরাঈলী ইহুদীবাদ গ্রহণ করেছিল তারাও এর মধ্যে ছিল। কুরআন মজীদে যেখানে বনী ইসরাঈল জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে সেখানে “হে বনী ইসরাঈল” বলা হয়েছে। আর যেখানে ইহুদী ধর্মের অনুসারীদের সম্বোধন করা হয়েছে সেখানে الَّذِينَ هَادُوا বলা হয়েছে।
১১. কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের এই দাবী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমনঃ তারা বলেন, ইহুদীরা ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না। (আল বাকারাহঃ ১১১) দোযখের আগুন আমাদের কখনো স্পর্শ করতে না। আর আমাদেরকে যদি নিতান্তই শাস্তি দেয়া হয় তাহলে মাত্র কয়েক দিনের জন্য দেয়া হবে (আল বাকারাহঃ ৮০; আলে ইমরানঃ ২৪) আমরা আল্লাহর বেটা এবং তাঁর প্রিয়পাত্র (আল মায়িদাহঃ ১৮) ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থসমূহেও এ ধরনের কিছু দাবী-দাওয়া দেখা যায়। সারা বিশ্বে অন্তত এতটুকু কথা জানে যে, তারা নিজেদেরকে আল্লাহর বাছাই করা সৃষ্টি বলে থাকে। তারা এরূপ এক খোশ খেয়ালে মত্ত যে, তাদের সাথে খোদার একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে যা অন্য কোন মানব গোষ্ঠীর সঙ্গে নেই।
১২. এখানে কুরআন মজীদে একথাটি দ্বিতীয়বারের মত ইহুদীদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে। প্রথম সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছিল, এদের বলো, আল্লাহর কাছে সমস্ত মানুষকে বাদ দিয়ে আখেরাতকের ঘর যদি কেবল তোমাদের জন্যই নির্দিষ্ট থেকে থাকে আর এ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে মৃত্যু কামনা করো। কিন্তু যেসব অপকর্ম তারা করেছে তার কারণে তারা কখনো মৃত্যু করবে না। আল্লাহ জালেমদের খুব ভাল করেই জানেন। বরং তোমরা দেখবে তারা কোন না কোন কোনভাবে বেঁচে থাকতে সমস্ত মানুষের চেয়ে এমনকি মুশরিকদের চেয়েও বেশী লালায়িত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আকাঙ্ক্ষা করে হাজার বছর বেঁচে থাকার। অথচ দীর্ঘ আয়ূ লাভ করলেও তা তাদেরকে এই আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবেনা। তাদের সমস্ত কৃতকর্মেই আল্লাহর দৃষ্টিতে আছে (আয়াতঃ ৯৪-৯৬) এ কথাটিই এখানে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এটা শুধু পুনরুক্তিই নয়। সূরা আল বাকারাহ-এর আয়াত গুলোতে একথা বলা হয়েছে। তখন, যখন ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের কোন যুদ্ধ হয়নি। কিন্তু এই সূরায় তার পুনরুক্তি করা হয়েছে এমন এক সময় যখন তাদের সাথে ইতিপূর্বে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর আরবভুমিতে চূড়ান্তভাবে তাদের শক্তি চূর্ণ করা হয়েছে। পূর্বে সূরা আল বাকারায় যে কথা বলা হয়েছিল এসব যুদ্ধ এবং তাদের পরিণাম অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষন দুই ভাবেই তা প্রমাণ করে দিয়েছিল। মদীনা এবং খায়বারে সংখ্যার দিক দিয়ে ইহুদী শক্তি কোনভাবেই মুসলমানদের তুলনায় কম ছিল না এবং উপায়-উপকরণ ও তাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। তাছাড়া আরবের মুশরিকদের ধ্বংস করার জন্য তারা মুনাফিকরাও তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করছিল। কারণ মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য তারা বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু এই অসম মোকাবিলায় যে জিনিসটি মুসলমানদের বিজয়ী এবং ইহুদীদের পরাজিত করেছিল তা ছিল এই যে, মুসলমানগণ আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করতে ভীত হওয়া তো দূরের কথা বরং হৃদয়ের গভীর থেকে মৃত্যু কামনা করতো এবং মরণপণ করে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তো। কারণ, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তারা আল্লাহর পথে লড়াই করছে। আর এ বিষয়ে ও পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, এ পথে শাহাদাত বরণকারীর জন্য রয়েছে জান্নাত। অপরদিকে ইহুদীদের অবস্থা ছিল এই যে, তারা কোন পথেই জান দিতে প্রস্তুত ছিল না; না খোদার পথে, না নিজের কওমের পথে এবং না নিজের জান, মাল ও ইজ্জত রক্ষার পথে। যে ধরনের জীবনই হোক না কেন তাদের প্রয়োজন ছিল কেবল বেঁচে থাকার। এ জিনিসটিই তাদেরকে ভীরু ও কাপুরুষ বানিয়ে দিয়েছিল।
﴿وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُۥٓ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّـٰلِمِينَ﴾
৭। তাহলে মৃত্যু চেয়ে নাও। কিন্তু যেসব অপকর্ম তারা করেছে ১৩ তার কারণে তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ এসব জালেমকে খুব ভালভাবেই জানেন।
১৩. অন্য কথায় মৃত্যু থেকে তাদের এই পালানো বিনা কারণে নয়। মুখে তারা যত বড় বড় কথাই বলুক না কেন, আল্লাহর দ্বীনের সাথে তারা যে আচরণ করেছে এবং পৃথিবীতে তারা যা করেছে আখেরাতে সেই সব আচরণ ও কাজকর্মের কিরূপ ফলাফল আশা করা যায় তাদের জ্ঞান ও বিবেক তা ভাল করেই জানতো। এ কারণে তাদের প্রবৃত্তি আল্লাহর আদালতের মুখোমুখি হতে টালবাহানা করে।
﴿قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَـٰقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَـٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾
৮। তাদের বলো, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাচ্ছো তা তোমাদের কাছে আসবেই তারপর তোমাদেরকে সেই সত্তার সামনে পেশ করা হবে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন। তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন যা তোমরা করছিলে।
﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌۭ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
৯। হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছো, জুমআ’র দিন১৪ যখন নামাযের জন্য তোমাদের ডাকা হয় তখন আল্লাহর যিকরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও।১৫ এটাই তোমাদের জন্য বেশী ভাল যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে।
১৪. এ আয়াতে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। প্রথমটি হলো, এতে নামাযের জন্য ঘোষণা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হলো, এমন একটি নামাযের জন্য ঘোষণা দেয়ার কথা আছে যা বিশেষভাবে শুধু জুমআর দিনেই পড়তে হবে। তৃতীয়টি হলো এই দু’টি জিনিসের কথা এভাবে বলা হয়নি যে, তোমরা নামাযের জন্য ঘোষণা করো এবং জুমআর দিনে একটি বিশেষ নামায পড়। বরং বর্ণনাভঙ্গী ও পূর্বাপর বর্ণনা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, নামাযের ঘোষণা এবং জুমআর দিনের বিশেষ নামায উভয়টিই আগে থেকেই চালু ছিল। তবে মানুষ ভুল করতো এই যে, জুমআর নামাযের ঘোষণা শুনেও তারা নামাযের জন্য দ্রুত অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে গাফলতি করতো এবং কেনাবেচার কাজেই ব্যস্ত থাকতো। তাই আল্লাহ তাআ’লা এ আয়াতটি শুধু এ উদ্দেশ্যে নাযিল করেছেন যে, মানুষ এই ঘোষণা এবং এই বিশেষ নামাযের গুরুত্ব উপলব্ধি করুক এবং ফরয মনে করে এবং উদ্দেশ্যে দ্রুত অগ্রসর হোক। এ তিনটি বিষয়ে যদি গভীরভাবে চিন্তা করা যায় তাহলে তা থেকে এই মৌলিক, বাস্তবতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআ’লা রাসূলুল্লাহ সা.কে এমন কিছু নির্দেশও দিতেন যা কুরআনের মধ্যে নেই। কিন্তু সেই সব নির্দেশ ও কুরআনের নির্দেশাবলীর মত অবশ্য পালনীয় ছিল। বর্তমানে গোটা পৃথিবীর প্রতিটি মসজিদে প্রতিদিন পাঁচবার যে আযান দেয়া হয় সেই আযানই নামাযের জন্য ঘোষণা। কিন্তু কুরআন মজীদের কোন স্থানে না এ আযানের ভাষা উল্লেখ করা হয়েছে, না মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, নামাযের জন্য এভাবে আহবান জানাও। এটি রাসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক নির্ধারিত জিনিস। কুরআন মজীদে শুধু দু’টি স্থানে একে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা হয়েছে। প্রথমত এই আয়াতে। দ্বিতীয়ত সূরা আল মায়িদার ৫৮ আয়াতে। অনুরূপ সারা দুনিয়ার মুসলমান আজ যে জুমআ’র নামায পড়ে থাকে কুরআন মজীদে তারও কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি এবং পড়ার সময় ও নিয়ম-পদ্ধতিও বলে দেয়া হয়নি। এ নামায পড়ার নিয়ম-পদ্ধতিও রাসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক চালু করা। কুরআনে এ আয়াতটি শুধু এর গুরুত্ব এবং অলংঘনীয়ভাবে পালন করার বিষয়টি বুঝানোর জন্যই নাযিল হয়েছে। স্পষ্ট এই দলীল থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বলে যে, শুধু কুরআনে বর্ণিত হুকুম-আহকামেই শরয়ী হুকুম-আহকাম-সে প্রকৃতপক্ষে শুধু সুন্নাতকেই অস্বীকার করে না, কুরআনকেও অস্বীকার করে।
এ বিষয়ে আরো বক্তব্য পেশ করার পূর্বে জুমআ’ সম্পর্কে আরো কয়েকটি বিষয়ও জেনে নেয়া দরকার।
জুমআ’ কথাটি প্রকৃতপক্ষে একটি ইসলামী পরিভাষা। জাহেলী যুগে আরবের অধিবাসীরা একে ‘ইয়াওমে আরূবা’ বলত। ইসলামী যুগে এ দিনটিকে মুসলমানদের সমাবেশের দিন হিসেবে নির্ধারিত করে এর নাম দেয়া হয় জুমআ’। ঐতিহাসিকগণ যদিও বলেন যে, কা’ব ইবনে লুয়াই কিংবা কুসাই ইবনে কিলাবও এদিনটির জন্য এ নাম ব্যবহার করেছিল। কারণ এ দিনেই তারা কুরাইশদের লোকজনের সমাবেশ করতেন (ফতহুল বারী)। কিন্তু তার এই কাজ দ্বারা প্রাচীন এই নামের কোন পরিবর্তন হয়নি। বরং সাধারণ আরবাসী এ দিনটিকে ‘আরূবা’ই বলত। সত্যিকার অর্থে নামের পরিবর্তন হয় তখন যখন ইসলামী যুগে এর নতুন রাখা হয়।
ইসলাম-পূর্ব যুগে সপ্তাহে একটি দিনকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা এবং তাকে জাতির প্রতীক হিসেবে নির্ধারিত করার রীতি আহলে কিতাবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইহুদীরা ঐ উদ্দেশ্যে ‘সাবতের(শনিবার) দিনটিকে নির্ধারিত করেছিল। কারণ আল্লাহ তাআ’লা এ দিনেই বনী ইসরাঈল জাতিকে ফেরাউনের গোলামী থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। খৃস্টানরা নিজেদেরকে ইহুদীদের থেকে আলাদা করে দেখানোর জন্য রবিবার দিনকে তাদের জাতীয় প্রতীক হিসেবে নির্ধারিত করে। যদিও এ সম্পর্কিত কোন নির্দেশ না হযরত ঈসা আ. দিয়েছিলেন না ইনজীল তথা বাইবেলে এর কোন উল্লেখ আছে। তবে খৃস্টানদের বিশ্বাস হলো ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে প্রাণ উৎসর্গ করার পর এ দিনেই হযরত ঈসা আ. কবর থেকে বেরিয়ে আসমানের দিকে গিয়ে ছিলেন। এ কারণেই পরবর্তীকালে খৃস্টানরা এ দিনটিকে তাদের উপাসনার দিন হিসেবে গ্রহণ করে। তারপর ৩২১ খৃস্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্য একটি নির্দেশের দ্বারা এ দিনটিকে সাধারণ ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করে। এ দু’টি জাতি থেকে নিজ জাতিকে আলাদা করার জন্য ইসলাম এ দু’টি দিন বাদ দিয়ে জুমআ’র দিনকে সামষ্টিক ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করেছে।
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবু মাসউ’দ আনসারীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, হিজরাতের কিছুকাল পূর্বে পবিত্র মক্কাতেই নবী সা. এর ওপর জুমআ’র ফরয হওয়ার বিধান নাযিল হয়। কিন্তু সে সময় তিনি এ নির্দেশের ওপর আমল করতে পারতেন না। কারণ মক্কায় সামষ্টিক কোন ইবাদাত করা সম্ভব ছিল না। তাই যেসব লোক নবীর সা. আগে মদীনায় হিজরত করেছিলেন তিনি তাদের নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যে, তারা যেন সেখানে জুমআ’ কায়েম করে। অতএব প্রথম দিকে হিজরাতকারীদের নেতা হযরত মুস’আব ইবনে উমায়ের ১২ জন লোক নিয়ে মদীনায় সর্বপ্রথম জুমআ’র নামায আদায় করেন। (তাবারানী, দারু কুতনী)। হযরত কা’ব ইবনে মালেক এবং ইবনে সিরীনের বর্ণনা মতে এরও পূর্বে আনসারগণ আপনা থেকেই (রাসূলুল্লাহ সা. এর নির্দেশ পৌঁছার পূর্বে) সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তারা সবাই মিলে সপ্তাহে একদিন সামষ্টিকভাবে ইবাদাত করবেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা ইহুদীদের সাবত এবং খৃস্টানদের রবিবার বাদ দিয়ে জুমআ’র দিনকে মনোনীত করেছিলেন এবং বনী বায়দা এলাকায় হযরত আসআদ ইবনে যুরারা প্রথম জুমআ’ পড়েছিলেন। এতে ৪০ ব্যক্তি শরীক হয়েছিল (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান, আবদ ইবনে হুমায়েদ, আবদুর রাযযাক, বায়হাকী)। এ থেকে জানা যায় ইসলামী জনতার আবেগ অনুভূতি তখন এমন একটি দিন থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিল যেদিন অধিক সংখ্যক মুসলমান একত্র হয়ে সামষ্টিকভাবে ইবাদাত করবে। তা শনিবার ও রবিবার থেকে আলাদা কোন দিন হওয়াটিও ইসলামী রুচি ও মেজাজ-প্রকৃতিরই দাবী ছিল। যাতে মুসলমানদের জাতীয় প্রতীক ইহুদী ও খৃস্টানদের জাতীয় প্রতীক থেকে আলাদা থাকে। এটা সাহাবা কিরামের ইসলামী মানসিকতার একটি বিস্ময়কর কীর্তি। অনেক সময় নির্দেশ আসার পূর্বে তাদের এই রুচি ও মেজাজ-প্রকৃতিই বলে দিতো যে, ইসলামের মেজাজ ও প্রকৃতি অমুক জিনিসের দাবী করছে।
হিজরত করার পর রাসূলুল্লাহ সা. সর্বপ্রথম যে কাজগুলো করেন জুমআ’র নামায কায়েম করা তার অন্যতম। পবিত্র মক্কা নগরী থেকে হিজরত করে সোমবার দিন তিনি কুবায় উপনীত হন, চারদিন সেখানে অবস্থান করেন এবং পঞ্চম দিন জুমআ’র দিনে সেখানে থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে বনী সালেম ইবনে আওফের এলাকায় জুমআ’র নামাযের সময় হয়। সেখানেই তিনি প্রথম জুমআ’র নামায পড়েন। (ইবনে হিশাম)।
এ নামাযের জন্য রাসূলুল্লাহ সা. সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার পরের সময় নির্দিষ্ট করেছিলেন অর্থাৎ ঠিক যোহরের নামাযের সময়। হিজরাতের পূর্বে হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরকে তিনি যে লিখিত নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেনঃ فَاِذَا مَالَ النَّهَارَ عَنْ شَطْرِهِ ،عِنْدَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ ، فَتَقَرَّبُوْا إِلَى اللهِ تَعَالَى بِرَكْعَتَيْنِ “জুমআ’র দিন সূর্য যখন মাথার ওপর থেকে পশ্চিম দিকে হেলে পড়বে তখন দুই রাকআত নামাযের সাহায্যে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর।” (দারু কুতনী)।
হিজরাতের পরে তিনি মৌখিকভাবেও এ নির্দেশ দিয়েছেন এবং কার্যতও ঐ সময়ে জুমআ’র নামায পড়াতেন। হযরত আনাস রা. হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রা., হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা., হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা., হযরত সাহল রা. ইবনে সা’দ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউ’দ, রা., হযরত আম্মার রা. ইবনে ইয়াসির এবং হযরত বেলাল রা., থেকে হাদীস গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। ঐ সব বর্ণনায় আছে সূর্য মাথার ওপর থেকে হেলে পড়ার পর নবী সা. জুমআ’র নামায পড়তেন। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী)।
নবী সা. এর কাজ-কর্ম থেকে এ বিষয়টিও প্রমাণিত যে, জুমআ’র দিন তিনি যোহরের নামাযের পরিবর্তে জুমআ’র নামায পড়াতেন। এ নামায ছিল মাত্র দু’রাকআত। নামাযের আগে তিনি খুতবা দিতেন। এটা ছিল জুমআ’র নামায এবং অন্যান্য দিনের যোহরের নামাযের মধ্যে পার্থক্যসূচক। হযরত উমর রা. বলেনঃ
صَلَاة الْمُسَافِر رَكْعَتَانِ, وصَلَاةِ الْفَجْرِ رَكْعَتَانِ, وَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِىِّكم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا قُصِرَتْ الْجُمُعَةُ لاَجْلِ الْخُطْبَةِ(احكام القران للجصاص)
“তোমাদের নবী সা. এর মুখ নিসৃতবাণী অনুসারে মূসাফিরের নামায দুই রাকআত, ফজরের নামায দু রাকআত এবং জুমআর নামায দুই রাকআত। এটা কসর নয়, বরং পূর্ণ নামায। আর খোতবা থাকার কারণে জুমআ’র নামায সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।”
এখানে যে আযানের উল্লেখ করা হয়েছে তা খোতবার বেশ আগে যে আযানের মাধ্যমে মানুষকে জুমআ’র নামাযের সময় আরম্ভ হওয়ার বিষয়টি অবগত করা হয় সে আযান নয়, বরং খোতবার ঠিক আগে যে আযান দেয়া হয় সেই আযান। হযরত সায়েব রা. ইবনে ইয়াযীদ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. এর যুগে শুধু একটি আযান দেয়া হতো। আর তা দেয়া হতো ইমাম মিম্বরে উঠে বসার পর। হযরত আবু বকর রা. ও হযরত উমরের রা. যুগেও এ কাজটিই করা হয়েছে। অতঃপর হযরত উসমানের রা. সময়ে জনবসতি বৃদ্ধি পেলে তিনি আরো একটি আযান দেয়ানো শুরু করেন। মদীনার বাজারে অবস্থিত তাঁর যাওরা নামক বাড়ীতে এ আযান দেয়া হতো। (বুখারী, আবু দাউদ, নাসায়ী, তাবারানী)
১৫. এই নির্দেশের মধ্যে উল্লেখিত (যিকর) শব্দের অর্থ হচ্ছে খোতবা। কারণ, আযানের পরে নবী সা. প্রথম যে কাজটি করতেন তা ছিল খোতবা। তিনি সবসময় খোতবার পরে নামায পড়াতেন। হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেনঃ “জুমআ’র ফেরেশতাগণ নামাযের জন্য আগমণকারী ব্যক্তির নাম তাদের আগমনের পরম্পরা অনুসারে লিখতে থাকেন। অতঃপরاذا خرج الامام حضرت الملئكة يسمعون الذكر ইমাম যখন খোতবার জন্য দাঁড়ান তখন তাঁর নাম লেখা বন্ধ করে দেন এবং যিকর (অর্থাৎ খোতবা) শুনতে মনোনিবেশ করেন” (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী।)। এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, যিকর অর্থ খোতবা। কুরআনের বর্ণনাভঙ্গী থেকেও এ অর্থের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কুরআনে প্রথমে বলা হয়েছেঃ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ “আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হও।” পরে বলা হয়েছেঃ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ “তারপর নামায শেষ হয়ে গেলে ভু-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ো।” এ থেকে জুমআ’র দিনের কাজের যে পরম্পরা বুঝা যায় তা হচ্ছে প্রথম আল্লাহর যিকির এবং তারপর নামায। মুফাসসিরগণও এ বিষয়ে একমত যে, যিকির অর্থ হয় খোতবা, নয়তো খোতবা ও নামায উভয়টাই।
খোতবার জন্য ذكر الله (যিকরুল্লাহ-আল্লাহর যিকির) শব্দ ব্যবহার করায় আপনা থেকেই এ অর্থ প্রকাশ পায় যে, খোতবার মধ্যে এমন সব বিষয় থাকতে হবে যা আল্লাহর স্মরণের সাথে সম্পর্কিত। যেমনঃ আল্লাহর তারিফ ও প্রশংসা ও তাঁর রাসূলের প্রতি দরুদ ও সালাত, তাঁর হুকুম আহকাম তাঁর শরীয়াত অনুসারে আমলের শিক্ষা ও উপদেশ এবং তাঁকে ভয় করেন এমন সব নেক বান্দাদের প্রশংসা ইত্যাদি। এ কারণে যামাখশারী কাশশফে লিখেছেন যে, খোতবার জালেম শাসকদের তারিফ ও প্রশংসা করা কিংবা তাদের নাম উল্লেখ করা এবং তাদের জন্য দোয়া করার “যিকরুল্লাহ”র সাথে দূরতম সম্পর্কেও নেই। বরং তা “যিকরুশ শাইতান”-শয়তানের যিকির হিসেবে পরিগণিত।
“আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হও, অর্থাৎ দৌড়িয়ে আসা নয়। বরং এর অর্থ হলো, তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছার চেষ্টা করো। আমাদের ভাষায়ও আমরা এ ধরনের অনেক কথা বলে থাকি। এসব কথার অর্থ হয়ে থাকে তৎপরতা দেখানো। দৌড়ানো অর্থে তা ব্যবহার করা হয় না। অনুরূপ আরবীতেও سعى শব্দ দ্বারা শুধু দৌড়ানোই বুঝায় না। কুরআনের অধিকাংশ স্থানে سعى শব্দটি প্রচেষ্টা চালানো এবং চেষ্টা-সাধনা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ
لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى- وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا – فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ – وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا
মুফাসসিরগণও সর্বসম্মতভাবে এ শব্দটিকে গুরুত্ব আরোপ করা অর্থে গ্রহণ করেছেন তাঁদের মতে سعى অর্থ হলো, আযান শোনার পর মানুষ অবিলম্বে মসজিদে পৌঁছার চিন্তা করতে থাকবে। ব্যাপারটা শুধু এতটুকু নয়, বরং নামাযের জন্য দৌড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেনঃ নামায শুরু হলে ধীরে সুস্থে ও স্থিরচিত্তে গাম্ভীর্যের সাথে নামাযে শরীক হওয়ার জন্য অগ্রসর হও, দৌড়িয়ে শরীক হয়ো না। এভাবে অগ্রসর হয়ে যতটা নামায পাবে তাতে শরীক হবে এবং যতটা ছুটে যাবে তা পরে পূরণ করে নেবে। (সিহাহ সিত্তাহ) হযরত আবু কাদাতা আনসারী রা. বলেনঃ একবার আমরা নবীর সা. সাথে নামায পড়ছিলাম। হঠাৎ আমরা লোকজনের দৌড়দৌড়ি করে চলার শব্দ শুনতে পেলাম। নামায শেষ করে নবী সা. ঐ লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করলেন, এসব কিসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম? তারা বললঃ নামাযে শরীক হওয়ার জন্য আমরা দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে আসছিলাম। তিনি বললেন, এরূপ করবে না। যখনই নামাযে আসবে শান্তভাবে ও স্থিরচিত্তে আসবে। এভাবে ইমামের সাথে যতটা নামায পাওয়া যাবে পড়বে। আর যে অংশ ছুটে যাবে তা পরে পড়ে নেনে। (বুখারী, মুসলিম)।
‘কেনা-বেচা পরিত্যাগ করো’ কথাটার অর্থ শুধু কেনা-বেচাই পরিত্যাগ করা নয়, বরং নামাযের জন্য যাওয়ার চিন্তাও ব্যবস্থা ছাড়া অন্য আর সব ব্যস্ততা পরিত্যাগ করা। বিশেষভাবে বেচা-কেনার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে শুধু এজন্য যে, জুমআ’র দিন ব্যবসায় বাণিজ্য খুব জমে উঠতো। এই দিন আশেপাশের জনপদের লোকজন একস্থানে সমবেত হতো। ব্যবসায়ীরা তাদের পন্যদ্রব্য নিয়ে সেখানে পৌঁছত। লোকজনও তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়তো। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা কেবল কেনা-বেচা পর্যন্তই সীমিত নয়, অন্যান্য সব ব্যস্ততাও এর অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু আল্লাহ তাআ’লা পরিষ্কাভাবে ঐ সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তাই ফিকহবিদগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, জুমআ’র আযানের পর কেনা-বেচা এবং অন্য সবরকমের কাজ কারবার হারাম।
এ নির্দেশটি থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, জুমআ’র নামায ফরয। প্রথমত আযান শোনামাত্র জুমআ’র নামাযের জন্য যাওয়ার তাগাদাই তার প্রমাণ। তাছাড়া জুমআ’র নামাযের জন্য কেনা-বেচার মত একটা হালাল কাজ হারাম হয়ে যাওয়াও এর ফরয হওয়া প্রমাণ করে। উপরন্তু জুমআ’র দিন যোহরের ফরয নামায রহিত হয়ে যাওয়া এবং তার পরিবর্তে জুমআ’র নামায প্রতিষ্ঠিত হওয়াও এর ফরয হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। কারণ, কোন ফরয কেবল তখনই রহিত হয় যখন তার চেয়ে ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন ফরয তার স্থান পূরণ করে। বহু সংখ্যক হাদীসে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এসব হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা. জুমআ’র নামাযের জন্য কঠোরভাবে তাকীদ করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় তাকে ফরয বলে ঘোষণা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউ’দ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেনঃ আমার মন চায়, অন্য কাউকে আমার পরিবর্তে নামায পড়াতে দাঁড় করিয়ে দেই এবং নিজে গিয়ে সেসব লোকদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেই যারা জুমআ’র নামায পড়তে আসে না। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী)। হযরত আবু হুরাইরা রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, আমরা জুমআ’র খোতবায় নবীকে সা. একথা বলতে শুনেছিঃ মানুষের জুমআ’র নামায পরিত্যাগ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। অন্যথায় আল্লাহ তাদের মনের ওপর মোহর মেরে দেবেন এবং তারা গাফিল হয়ে যাবে। (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম, নাসায়ী)। হযরত আবুল জা’দ রা. দামরী, হযরত জাবের রা. ইবনে আবদুল্লাহ ও হযরত আবদুল্লাহ রা. ইবনে আবী আওফার বর্ণিত হাদীসসমূহে নবীর সা. যেসব বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে জানা যায়, “যে ব্যক্তি প্রকৃত কোন কারণ ও সঙ্গত ওযর ছাড়া শুধু বে-পরোয়া মানসিকতার কারণে পরপর তিনটি জুমআ’ পরিত্যাগ করে আল্লাহ তার দিলের ওপর মোহর মেরে দেন। বরং একটি হাদীসে তো এতদূর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআ’লা তার দিলকে মুনাফিকের দিল বানিয়ে দেন” (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজা, দারেমী, হাকেম, ইবনে হিব্বান, বাযযার, তাররানী ফিল কাবীর)। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেনঃ “আজ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের ওপর জুমআ’র নামায ফরয। যে ব্যক্তি তাকে মামুলি ব্যাপার মনে করে এবং তার গুরুত্ব স্বীকার না করে পরিত্যাগ করবে আল্লাহ যেন তার অবস্থা ভাল না করেন এবং তাকে কোন প্রকার বরকতও না দেন। কান পেতে শুণে নাও যতক্ষণ সে তাওবা না করবে তার নামায নামায নয়, তার যাকাত যাকাত নয়, তার হজ্জ হজ্জ নয়, তার রোযা রোযা নয়, তার কোন নেক কাজ নেক কাজ নয়। অতঃপর যে তাওবা করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমাকারী।” (ইবনে মাজা, বাযযার) প্রায় একই অর্থের একটি হাদীস তাবারানীতার ‘আওসাত’গ্রন্থে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও বহু সংখ্যক হাদীসে নবী সা. স্পষ্ট ভাষায় জুমআ’র নামাযকে ফরয এবং অবশ্য পালনীয় হক বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. ইবনে আস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেনঃ যারা আযান শুনতে পায় জুমআ’র নামায তাদের ওপরই ফরয (আবু দাউদ, দারুকুতনী)। জাবের রা. ইবনে আবদুল্লাহ ও আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেনঃ “জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের উপর জুমআ’র নামায ফরয করেছেন” (বায়হাকী)। তবে তিনি নারী, শিশু, ক্রীতদাস, অসুস্থ ব্যক্তি এবং মূসাফিরকে এ ফরয পালনের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিয়েছেন। হযরত হাফসা বর্ণনা করেন যে, নবী সা. বলেছেনঃ “জুমআ’র নামাযের জন্য বের হওয়া প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব।”(নাসায়ী)। হযরত তারেক ইবনে শিহাব বর্ণিত হাদীসে নবী সা. বলেছেনঃ ক্রীতদাস, নারী, শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া জামায়াতের সাথে জুমআ’ পড়া প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব, (আবু দাউদ ও হাকেম।)। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত হাদীসে নবীর সা. ভাষ্য হলোঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে তার ওপরে জুমআ’ ফরয। তবে নারী, মূসাফির, ক্রীতদাস, বা অসুস্থ ব্যক্তির ওপরে জুমআ’ ফরয নয়। (দারু কুতনী, বায়হাকী)। কুরআন ও হাদীসের এই স্পষ্ট বক্তব্যের ভিত্তিতে জুমআ’র নামায ফরয হওয়া সম্পর্কে গোটা মুসলিম উম্মাহ ইজমা বা ঐকমত্য পোষণ করেছেন।
﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًۭا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
১০। তারপর যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো১৬ এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো।১৭ আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।১৮
১৬. একথার অর্থ এ নয় যে, জুমআ’র নামায পড়ার পর ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়া বা রিযিকের অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে উঠা জরুরী। বরং এ নির্দেশ থেকে শুধু এ কাজ করার অনুমতি বুঝায়। যেহেতু জুমআ’র আযান শোনার পর সব কাজ কর্ম পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তাই বলা হয়েছে, নামায শেষ হওয়ার পর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার এবং যে কাজ-কর্ম করতে চাও তা করার অনুমতি তোমাদের জন্য আছে। এটা ঠিক ইহরাম অবস্থায় শিকার নিষিদ্ধ করার পরوَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا “যখন ইহরাম খুলবে তখন শিকার করো” (আল মায়িদাহঃ ৩) বলার মত। এ কথার অর্থ এটা নয় যে, ইহরাম খোলার পর অবশ্যই শিকার করতে হবে। বরং এর অর্থ হলো, ইহরাম খোলার পর শিকার করার ব্যাপারে আর কোন বাধা নিষেধ থাকে না। কিংবা সূরা আন নিসাতে যেমন فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ আয়াতাংশে একাধিক বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এখানে যদিও নির্দেশসূচক শব্দ فَانْكِحُوا ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু কেউ-ই একে নির্দেশ অর্থে গ্রহণ করেননি। এর থেকে মৌলিক একটি মাসায়ালার তথা সূত্র পাওয়া যায় যে, আদেশসূচক শব্দ দ্বারা সবসময় কোন জিনিস ওয়াজিব বা অবশ্য পালনীয় বলে প্রমাণিত হয় না। বরং তা কখনো অনুমতি আবার কখনো কোন জিনিসকে তুলনামূকভাবে বেশী পছন্দ করা অর্থ বুঝায়। এক্ষেত্রে কোথায় তা আদেশ অর্থে, কোথায় অনুমতি অর্থে এবং কোথায় আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় হওয়া অর্থে ব্যবহার হয়েছে সে বিষয়টি আগের ও পরের প্রসঙ্গ থেকে বুঝা যায়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই যে কাজটি ফরয বা ওয়াজিব সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এ আয়াতাংশের ঠিক পরের আয়াতাংশেই বলা হয়েছে وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا “আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করো।” এখানেও আদেশসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ শব্দ ওয়াজিব বা অবশ্য করণীয় অর্থ প্রকাশ করছে না, বরং “পছন্দনীয় হওয়া” অর্থ প্রকাশ করছে। এখানে এ বিষয়টিও উল্লেখ্য যে, কুরআনে যদিও ইহুদীদের সাবত এবং খৃস্টানদের রোববারের মত জুমআ’র দিনকে সাধারণ ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়নি, কিন্তু একথা কেউ-ই অস্বীকার করতে পারে না যে, শনিবার ও ররিবার ইহূদী ও খৃস্টানদের জাতির প্রতীক জুমআ’ও ঠিক তেমনি মুসলমানদের জাতির প্রতীক। সুতরাং তামাদ্দুনিক বা সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে যদি সপ্তাহের কোন দিনকে সাধারণ ছুটির জন্য মনোনীত করতে হয় তহলে ইহুদীরা যেমন স্বাভাবিকভাবে শনিবারকে এবং খৃস্টানরা রোববারকে বেছে নিয়েছে তেমনি এ উদ্দেশ্যে মুসলমানরাও (যদি তাদের মন-মানস ও স্বভাব প্রকৃতিতে লেশমাত্র ইসলামী অনুভূতি বিদ্যমান থেকে থাকে) জুমআ’র দিনকেই বেছে নেবে। খৃস্টানরা তো তাদের নিজের দেশ ছাড়া এমনসব দেশের ওপরও তাদের রোববার চাপিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি। যেখানে খৃস্টানদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য ছিল। ইহুদীরা ফিলিস্তিনে তাদের ইসরাঈলী রাষ্ট্র কায়েম করলে সর্বপ্রথম যে কাজটি করেছিল তা হচ্ছে রোববারের পরিবর্তে শনিবারকে ছুটির দিন হিসেবে নির্ধারিত করা। বিভাগ পূর্ব ভারতে বৃটিশ ভারত এবং মুসলিম দেশীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে যে উল্লেখ্যযোগ্য পার্থক্য নজরে পড়ত তা হচ্ছে দেশের এক অংশে রোববারে সাপ্তাহিক ছুটি হতো এবং অন্য অংশে জুমআ’র দিনে ছুটি হতো। তবে যেসব জায়গায় মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী অনুভূতি ও ভাবধারা বর্তমান থাকত না সেখানে ক্ষমতা নিজেদের হাতে আসার পরও তারা রোববারকেই বুকে জড়িয়ে রাখে যা আমরা পাকিস্তানে দেখতে পাচ্ছি। আর চেতনাহীনতার মাত্রা এর চেয়েও অধিক হলে জুমআ’র দিনের সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল করে রোববার দিন সাপ্তাহিক ছুটি চালু করা হয়। মুস্তাফা কামাল তুরস্কে এ কাজটিই করেছেন।
১৭. অর্থাৎ নিজেদের কাজ-কর্ম ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যস্ত হয়েও আল্লাহকে ভুলে যেও না। বরং সর্বাবস্থায় তাঁকে স্মরণে রাখো এবং তাঁকেই স্মরণ করতে থাকো। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আহযাবঃ টীকা ৬৩)
১৮. কুরআন মজীদে বেশ কিছু সংখ্যক জায়গায় একটি হিদায়াত বা দিক নির্দেশনা, কিংবা একটি উপদেশ অথবা একটি নির্দেশ দেয়ার পর لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (হয়তো তোমরা সফল হবে, কল্যাণ লাভ করবে) এবং لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (হয়ত তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে) বলা হয়েছে। এসব স্থানে ‘হয়ত’ বা ‘সম্ভবত’ শব্দ ব্যবহার করার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তাআ’লার (মাআ’যাল্লাহ) কোন সন্দেহ আছে। মূল ব্যাপার তা নয়। বরং এটি একটি রাজকীয় বর্ণনাভঙ্গি। এটা ঠিক তেমন যেন কোন দয়ালু মনিব তাঁর কর্মচারীকে বলছেন, তুমি অমুক কাজটি করো, হয়তো তোমার পদোন্নতি হবে। এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম অদৃশ্য প্রতিশ্রুতি থাকে যার আশায় কর্মচারীটি মনযোগ দিয়ে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে ঐ কাজটি আঞ্জাম দিতে থাকে। কোন বাদশাহর মুখ থেকে তার কোন কর্মচারীর উদ্দেশ্যে একথা উচ্চারিত হলে তার ঘরে খুশীর বন্যা বয়ে যায়।
এখানে যেহেতু, জুমআ’র নামাযের হুকুম-আহকাম বর্ণনা শেষ হয়ে গিয়েছে, তাই কুরআন, হাদীস, সাহাবীদের উক্তি এবং ইসলামের সাধারণ মূলনীতির আলোকে চারটি ফিকহী মাযহাবের জুমআ’র নামায সম্পর্কে যেসব হুকুম-আহকাম বের করে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে এখানে তার সারসংক্ষেপ বর্ণনা করা সমীচীন হবে বলে মনে হয়।
হানাফী মাযহাবের মতে যোহরের নামাযের সময়ই জুমআ’র নামাযের সময়। জুমআ’ এ সময়ের পূর্বেও পড়া যেতে পারে না, পরেও পড়া যেতে পারে না। প্রথম আযানের সময় থেকেই কেনা-বেচা হারাম হয়ে যায়,-ইমাম মিম্বরের ওপর বসার পর দ্বিতীয় আযান দেয়ার সময় থেকে নয়। কারণ, কুরআনে শুধু إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ কথাটি বলা হয়েছে। তাই সূর্য মাথার ওপর থেকে পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ার পর যখন জুমআ’র সময় শুরু হয় তখন জুমআ’র নামাযের যে আযানটিই দেয়া হোক না কেন তা শোনার পর লোকদের কেনা-বেচা বন্ধ করে দেয়া কর্তব্য। তবে সেই সময় যদি কোন ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করে তবে সেই ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ বা বাতিল হবে না, বরং তা কেবল একটি গোনাহের কাজ হবে। জুমআ’র নামায প্রতিটি জনপদেই অনুষ্ঠিত হবে না, বরং শুধু مصر جامع “মিসরে জামে”-তে অনুষ্ঠিত হতে পারবে। নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা অনুসারে ‘মিসরে জামে’ বলা হয় এমন শহরকে যেখানে বাজার আছে, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা আছে এবং তার জনবসতিও এত যে, যাদের ওপর জুমআ’র নামায ফরয তারা সবাই যদি ঐ শহরের সর্বাপেক্ষা বড় মসজিদে সমবেত হয় তাহলে সেখানে স্থান সংকুলান হবে না। যেসব লোক শহরের বাইরে বসবাস করেন তাদের জন্য শহরে এসে জুমআ’র নামায পড়া কেবল তখনই ফরয যখন আযাবের শব্দ তারা শুনতে পাবে কিংবা খুব বেশী হলে শহর থেকে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত হবে। নামায মসজিদেই হতে হবে তা জরুরী নয়। নামায খোলা মাঠেও হতে পারে। এমন মাঠেও জুমআ’র নামায হতে পারে যা শহরের বাইরে অবস্থিত হলেও মূল শহরের একটি অংশ বলে বিবেচিত। যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির শরীক হওয়ার সাধারণ অনুমতি আছে শুধু সেখানেই জুমআ’র নামায অনুষ্ঠিত হতে পারে। কোন বন্ধ জায়গায় যত মানুষই একত্রিত হোক না কেন, সেখানে সবারই আসার অনুমতি না থাকলে, জুমআ’র সহীহ হবে না। জুমআ’র নামায সহীহ হওয়ার জন্য জামায়াতে [আবু হানীফার রাহি. মতে] ইমাম ছাড়া কমপক্ষে তিন জন অথবা [আবু ইউসুফ রাহি. ও মুহাম্মাদের মতে] ইমাম সহ দুইজন এমন লোক থাকতে হবে যাদের ওপর জুমআ’ ফরয। যেসব ওজর থাকলে জুমআ’ পড়া থেকে অব্যহতি পাওয়া যায় তা হচ্ছেঃ সফরে থাকা, অথবা এমন রুগ্ন হওয়া যে, নিজে হেঁটে মসজিদে আসার ক্ষমতা নেই। অথবা দু’টি পা-ই অক্ষম অথব অন্ধ, (কিন্তু ইমাম আবু ইউসূফ রাহি. ও মুহাম্মাদের রাহি. মতে অন্ধ ব্যক্তি কেবল তখনই জুমআ পড়া থেকে অব্যহতি পাবে যখন তাকে মসজিদে নিয়ে যাবার মত কোন লোক পাবে না।) অথবা কোন অত্যাচারীর পক্ষ থেকে তার জীবন ও মান-ইজ্জতহানীর কিংবা সহ্যসীমা বহির্ভূত আর্থিক ক্ষতিরআশঙ্কা থাকে অথবা প্রচণ্ড বৃষ্টি অথবা কাদা পানি থাকে অথবা যদি সে বন্দী থাকে। কয়েদী ও অক্ষমদের জন্য জুমআ’র দিনে যোহরের নামায জামায়াতে পড়া মাকরূহ। যারা জুমআ’র নামায পায়নি তাদের জন্য যোহরের নামায জামায়াতে পড়া মাকরূহ। খোতবা জুমআ’ সহীহ হওয়ার একটি শর্ত। কারণ, নবী কখনো খোতবা ছাড়া জুমআ’র নামায পড়েননি। আর খোতবা অবশ্যই দু’টি হতে হবে এবং নামাযের আগে হতে হবে। ব্যক্তি যে স্থানে বসে আছে সে স্থানে পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছুক আর না পৌঁছুক খোতবা দেয়ার জন্য ইমাম যখন মিম্বরের দিকে অগ্রসর হবেন তখন থেকে খোতবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবরকম কথাবার্তা নিষিদ্ধ। এই সময় নামাযও না পড়া উচিত। (হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কুরআন–জাসসাস আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া, উমদাতুল কারী)
শাফেয়ী মাযাহাবের মতে যোহরের নামাযের সময়ই জুমআ’র নামাযের সময়। যখন দ্বিতীয় আযান (অর্থাৎ ইমাম মিম্বরের ওপর বসার পর যে আযান দেয়া) হবে তখন থেকে কেনা-বেচা হারাম ও নামাযের জন্য যাওয়া ওয়াজিব। তা সত্ত্বেও কেউ যদি এ সময় কেনা-বেচা করে তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে না। এমন প্রত্যেকটি জনপদেই জুমআ’ অনুষ্ঠিত হতে পারবে যেখানকার স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে ৪০ জন লোক এমন আছে যাদের ওপর জুমআ’র নামায ফরয। জনপদের বাইরের যেসব এলাকার লোক আযান শুনতে পায় তাদের জন্য জুমআ’র নামাযে হাজির হওয়া অবশ্য কর্তব্য। জনবসতির অভ্যন্তরেই জুমআ’র নামায অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। তবে জরুরী নয় যে, তা মসজিদেই পড়তে হবে। যারা মরুভূমির মধ্যে তাঁবুতে অবস্থান করে তাদের ওপরে জুমআ’র ফরয নয়। জুমআ’ শুদ্ধ হওয়ার জন্য যাদের ওপর জুমআ’ ফরয ইমাম সহ কমপক্ষে এ রকম ৪০ জন লোকের জামায়াতে উপাস্থিত থাকা অবশ্যক। যেসব ওজর থাকার কারণে কোন ব্যক্তি জুমআ’র নামায পড়া থেকে অব্যহতি লাভ করে তা হচ্ছেঃ সফরে থাকা অথবা কোন স্থানে চারদিন বা তার কম সময় অবস্থান করার ইচ্ছা করা, তবে সফর বৈধ হতে হবে। এমন বৃদ্ধ বা রুগ্ন যে সওয়ারীতে চড়েও জুমআ’য় হাজির হতে অক্ষম। অন্ধ হওয়া এবং তাকে নামাযের জন্য মসজিদে নিয়ে যাওয়ার মত কোন লোক না পাওয়া। প্রাণ, সম্পত্তি অথবা-মান-ইজ্জাতহানীরআশঙ্কা থাকা। বন্দী অবস্থায় থাকা। তবে এই বন্দিদশা তার নিজের কোন অপরাধের কারণে না হওয়া। নামাযের পূর্বে দু’টি খোতবা থাকতে হবে। খোতবার সময় চুপচাপ থাকা সুন্নাত, তবে কথা বলা হারাম নয়। যে ব্যক্তি ইমামের এতটা কাছে বসেছে যে, খোতবা শুনতে পায় তার জন্য কথাবার্তা বলা মাকরূহ। তবে সে সালামের জবাব দিতে পারে এবং রাসূলুল্লাহ সা. এর নামের উল্লেখ শুনে উচ্চাস্বরে দরূদ পাঠ করতে পারে। (মুগনিউল মুহতাজ, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া)
মালেকী মাযাহাবের মতে জুমআ’র নামাযের সময় হচ্ছে সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার পর থেকে শুরু করে মাগরিবের এতটা পূর্ব পর্যন্ত যেন সূর্যাস্তের আগেই খোতবা ও নামায শেষ হয়ে যায়। কেনা-বেচা হারাম ও নামাযের জন্য যাওয়া ওয়াজিব হয় দ্বিতীয় আযান থেকে। এ সময়ের পর কোন কেনা-বেচা হলে তা অবৈধ ও বাতিল বলে গণ্য হবে। কেবল সেই সব জনপদেই জুমআ’ অনুষ্ঠিত হতে পারে যেখানকার অধিবাসীগণ স্থায়ীভাবে সেখানে বাসস্থান তৈরী করে বসবাস করছে। শীত গ্রীষ্মে তারা অন্য কোন স্থানে চলে যায় না। তারা ঐ জনপদেই তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছুর সরবরাহ পেয়ে থাকে এবং সংখ্যার দিক দিয়ে তারা নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করতে পারে। অস্থায়ী অবস্থান স্থলে যত লোকই থাক না কেন এবং তারা যতদিনই অবস্থান করুক না কেন সেখানে জুমআ’ অনুষ্ঠিত হতে পারে না যে জনপদে জুমআ’ অনুষ্ঠিত হয় তার তিন মাইল দূরত্বের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের ওপর জুমআ’র নামাযে হাজির হওয়া ফরয। জুমআ’র নামায কেবল এমন সব মসজিদেই অনুষ্ঠিত হতে পারে যা জনপদের ভিতরে বা সংলগ্নস্থানে অবস্থিত হবে এবং যার ইমরাত জনপদের সাধারণ অধিবাসীদের ঘরের চেয়ে নিম্নমানের হবে না। এক্ষেত্রে কোন কোন মালেকী ফিকাহবিদ এরূপ শর্তও আরোপ করেছেন যে, মসজিদ ছাদ বিশিষ্ট হতে হবে এবং তাতে যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যবস্থা নেই। যা কেবল জুমআ’র নামায পড়ার জন্য তৈরী করা হয়েছে। জুমআ’র নামায সহীহ হওয়ার জন্য যাদের ওপর জুমআ’র নামায ফরয ইমাম ছাড়া কমপক্ষে এ রকম ১২ জন লোকের জামায়াতে উপস্থিত থাকা জরুরী। যেসব ওজর বর্তমান থাকলে কোন ব্যক্তির ওপর থেকে জুমআ’র নামায পড়ার নির্দেশ রহিত হয়ে যায় তা হচ্ছেঃ সফলে থাকা অথবা সফর অবস্থায় কোন স্থানে চারদিনের কম সময় অবস্থানের নিয়ত করা। এমন রুগ্ন হওয়া যে, তার পক্ষে মসজিদে আসাই অসম্ভব। মা অথবা বাপ অথবা স্ত্রী অথবা সন্তান রুগ্ন ও অসুস্থ থাকা অথবা সে এমন কোন অপরিচিত রোগীর সেবা যত্ন করছে যার সেবা যত্ন করার মত আর কেউ নেই, অথবা তার কোন নিকটাত্মীয় কঠিন রোগে আক্রান্ত অথবা মরণাপন্ন। যে সম্পদের ক্ষতি সে বরদাশত করতে অক্ষম এমন সম্পদের ক্ষতিরআশঙ্কা থাকা। অথবা মারপিট ও বন্দীত্বের ভয়ে আত্মগোপন করে থাকা। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে তাকে মজলুম বা অত্যাচারিতের পর্যায়ভুক্ত হতে হবে। প্রচণ্ড বৃষ্টি বা কাদা পানি থাকা কিংবা প্রচণ্ড গরম বা ঠাণ্ডা মসজিদ পর্যন্ত যেতে বাধা হয়ে দাঁড়ালে। নামাযের পূর্বে দু’টি খোতবা হওয়া অত্যাবশ্যক। এমনকি খোতবা যদি নামাযের পরে দেয়া হয় তাহলে নামায পুনরায় পড়া জরুরী। খোতবা মসজিদের ভিতরে হতে হবে। খোতবা দেয়ার জন্য ইমাম যখন মিম্বরের দিকে অগ্রসর হবেন সেই সময় নফল নামায পড়া হারাম এবং খোতবা শুরু হলে তা শোনা না গেলেও কথাবার্তা বলাও হারাম। তবে খতীব যদি খোতবা বহির্ভুত কোন বাজে বা অপ্রয়োজনীয় কথা বলেন অথবা গালির উপযুক্ত নয় এমন কোন ব্যক্তিকে গালি দেন অথবা এমন কোন ব্যক্তির প্রশংসা করতে শুরু করেন যার প্রশংসা করা জায়েয নয়, অথবা খোতবার সাথে সম্পর্কহীন কোন কিছু পড়তে শুরু করেন তাহলে তার প্রতিবাদ করার অধিকার লোকজনের আছে। তাছাড়া জীবনেরআশঙ্কা না থাকলে বর্তমানে বাদশাহ বা শাসকের জন্য খোতবার মধ্যে দোয়া করাও মাকরূহ। যিনি নামায পড়াবেন তাঁকেই খোতবা দিতে হবে। খতীব ছাড়া অন্য কেউ নামায পড়ালে সে নামায বাতিল হয়ে যাবে। (হাশিয়াতুদ দুসুকী আলশ শারহিল কাবীর, আহকামুল কুরআন-ইবনে আরাবী, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া)
হাম্বলী মাযহাবের মতে জুমআ’র নামাযের সময় সকাল বেলা সূর্য কিছুটা ওপরে ওঠার পর থেকে আসরের সময় শুরু হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার আগে জুমআ’র নামায পড়া শুরু জায়েয এবং পরে ওয়াজিব ও উত্তম। দ্বিতীয় আযান থেকে কেনা-বেচা হারাম এবং নামাযের জন্য প্রস্তুত হওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। এরপর কেনা-বেচা হলে তা কেনা-বেচা হয়েছে বলে ধরা হবে না। যাদের ওপর জুমআ’র নামায ফরয এমন ৪০ জন লোক যে স্থানে আছে কেবল সেখানেই জুমআ’ অনুষ্ঠিত হতে পারে। এসব লোকের স্থায়ীভাবে বাড়ীঘরে (তাঁবুতে নয়) বসবাসকারী হতে হবে। অর্থাৎ শীত বা গ্রীষ্মকালে তারা কোথাও স্থানান্তরিত হয় না। এ জন্য জনবসতির বাড়ী ঘর ও মহল্লাসমূহ পরস্পর সংলগ্ন হোক বা বিচ্ছিন্ন হোক তাতে কোন পার্থক্য হয় না। এই জনপদের বিভিন্ন অংশের মধ্যকার দূরত্ব কয়েক মাইল হলেও যদি তা সমষ্টিগতভাবে একটি নামে পরিচিত হয় তাহলে তা একটি জনপদ বলে গণ্য হবে। এ ধরনের জনপদ থেকে যারা তিন মাইল দূরত্বের মধ্যে বসবাস করে তাদের জন্য জুমআ’র নামায পড়তে মসজিদে আসা ফরয। জামায়াতে ইমাম সহ ৪০ ব্যক্তির উপস্থিত থাকা জরুরী। নামায মসজিদেই হতে হবে এমনটি জরুরী নয়। বরং খোলা মাঠেও নামায হতে পারে। যেসব কারণ বর্তমান থাকলে কোন ব্যক্তির ওপর জুমআ’র নামায আর ফরয থাকে না তা হচ্ছেঃ মূসাফির হওয়া, যে জনপদের লোকদের ওপর জুমআ’ ফরয এমন জনপদে চারদিন বা তার কম সময় অবস্থানের ইচ্ছা করা, এমন রুগ্ন হওয়া যে সওরীতে উঠে মসজিদে আসাও অসসম্ভব, অন্ধ হওয়া-তবে সে নিজে যদি পথ হাতড়িয়ে আসতে পারে তাহলে আসবে। অন্য কোন লোকের সাহায্য নিয়ে অন্ধ ব্যক্তির জন্য মসজিদে আসা ওয়াজিব নয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বা গরম অথবা প্রচণ্ড বৃষ্টি বা কাদা নামাযের স্থানে পৌঁছতে প্রতিবন্ধক হওয়া। কোন জালেমের জুলুম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আত্মগোপন করে থাকা। প্রাণ ও মান-ইজ্জতহানিরআশঙ্কা কিংবা এমন আর্থিক ক্ষতিরআশঙ্কা থাকা যা বরদাশত করা যাবে না। নামাযের আগে দু’টি খোতবা হতে হবে। খতীবের কথা শোনা যায়, যে ব্যক্তি খতীবের এতটা নিকটে আছে খোতবার সময় তাঁর জন্য কথাবার্তা বলা হারাম। তবে দূরে অবস্থিত লোক যার কাছে খতীবের আওয়াজ পৌঁছে না সে কাথাবার্তা বলতে পারে। খতীব ন্যায়পরায়ন হোক বা না হোক খোতবার সময় সবার চুপচাপ থাকা উচিত। জুমআর দিনে ঈদ হলে যারা ঈদের নামায পড়বে তাদের জন্য জুমআ’র নামায পড়া ফরয নয়। এ বিষয়ে হাম্বলী মযহাবের মত তিন ইমামের মত থেকে ভিন্ন (গায়তুল মুনতাহা, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া)
যে ব্যক্তির ওপর জুমআ’ ফরয নয় সে যদি জুমআ’র নামাযে শরীক হয় তাহলে তার নামায সহীহ হবে এবং তার ওপর যোহরের নামায আর ফরয থাকবে না। এ বিষয়ে সমস্ত ফিকহবিদ একমত।
﴿وَإِذَا رَأَوْا۟ تِجَـٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًۭا ۚ قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌۭ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَـٰرَةِ ۚ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ﴾
১১। আর যে সময় তারা ব্যবসায় ও খেল তামাশার উপকরণ দেখলো তখন তারা তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে১৯ সেদিকে দৌড়ে গেল। তাদের বলো, আল্লাহর কাছে যা আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসায়ের চেয়ে উত্তম।২০ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।২১
১৯. যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জুমআ’র হুকুম-আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে এটিই সেই ঘটনা। হাদীস গ্রন্থসমূহে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত আবু মালেক এবং হযরত হাসান বসরী, ইবনে যায়েদ, কাতাদা এবং মুকাতিল ইবনে হাইয়ান থেকে ঘটনার যে বিবরণ বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছেঃ পবিত্র মদীনা নগরীতে সিরিয়া থেকে একটি বাণিজ্য কাফেলা ঠিক জুমআ’র নামাযের সময় এসে পৌঁছলো এবং জনপদের লোকজন যাতে তাদের আগমনের খবর জানতে পারে সেজন্য ঢোল-বাদ্য বাজাতে শুরু করলো। রাসূলুল্লাহ সা. সে সময় খোতবা দিচ্ছিলেন। ঢোল ও বাদ্য যন্ত্রের শব্দ শুনে সব মানুষ অস্থির হয়ে উঠল এবং ১২ জন লোক ছাড়া সবাই ‘বাকী’ নামক স্থানে ছুঁটে গেল। বাণিজ্য কাফেলা এখানেই অবস্থান করেছিল। এই ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা আছে। এর মধ্যে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর বর্ণনাটি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। এ বর্ণনাটিকে ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু উওয়ানা, আবদ ইবনে হুমাইদ, আবু ইয়ালা, প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সময়ে বর্ণনা করেছেন। এসব বর্ণনার মধ্যে অসামঞ্জস্য শুধু এতটুকু যে, কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে ঘটনাটি নামাযরত অবস্থায় ঘটেছিল। আবার কোন বর্ণনাতে বলা হয়েছে যে, নবী সা. যখন খোতবা দিচ্ছিলেন ঘটনাটি তখন ঘটেছিল। কিন্তু হযরত জাবের এবং অন্য সব সাহাবী ও তাবেয়ীদের সবগুলো বর্ণনা একসাথে বিচার করলে যে কথাটি সঠিক বলে মনে হয় তাহলো ঘটনাটি খোতবার সময় সংঘটিত হয়েছিল। যেখানে তিনি বলেছেন যে, ঘটনাটি জুমআ’র নামাযের সময় ঘটেছিল সেখানে তিনি জুমআ’র নামায বলতে খোতবা ও নামায উভয়ের সমষ্টিকে বুঝিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় বলা হয়েছে, সে সময় ১২ জন পুরুষের সাথে সাত জন মহিলাও রয়ে গিয়েছেন। (ইবনে মারদুইয়া) কাতাদা বর্ণনা করেছেন যে, ১২ জন পুরুষের সাথে ১ জন মহিলা ও ছিলেন। (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম)। দরুকুতনীর একটি রেওয়ায়াতে ৪০ ব্যক্তি এবং আবদ ইবনে হুমায়াদের রেওয়ায়াতে ৭ জন্যর কথা বলা হয়েছে। ফাররা, আটজনের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এগুলো সবই দুর্বল রেওয়ায়াত। কাতাদার এ রেওয়ায়াতও দুর্বল যে, এ ধরনের ঘটনা তিনবার ঘটেছিল। (ইবনে জারীর)। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর রেওয়ায়াতটিই নির্ভরযোগ্য। এতে মসজিদে থেকে যাওয়া লোকের সংখ্যা ১২ জন বলা হয়েছে। আর কাতাদার একটি রেওয়ায়াত ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত সাহাবী ও তাবেয়ীদের বর্ণনাসমূহ এ বিষয়ে একমত যে, এ ঘটনা মাত্র একবারই ঘটেছে। মসজিদে থেকে যাওয়া লোকদের সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়াত একত্রে বিচার করলে জানা যায়, তাদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবু বকর রা., হযরত উমর রা., হযরত উসমান রা., হযরত আলী রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউ’দ রা., হযরত আম্মার রা.। ইবনে ইয়াসির, হুযাফার আযাদ কৃতদাস হযরত সালেম রা. এবং হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ। হাফেস আবু ইয়ালা, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর যে রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন তাতে বলা হয়েছে। লোকজন যখন এভাবে বের হয়ে চলে গেল এবং মাত্র ১২ জন অবশিষ্ট থাকলেন তখন নবী সা. তাদের সম্বোধন করে বললেনঃ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْكُمْ أَحَدٌ لَسَالَ بِكُمُ الْوَادِىْ نَارًا
“তোমরা সবাই যদি চলে যেতে এবং একজনও অবশিষ্ট না থাকত তাহলে এ উপত্যকা আগুনের প্রবাহে প্লাবিত হয়ে যেত।”
ইবনে মারদুইয়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে এবং ইবনে জারীর কাতাদা থেকে প্রায় এর অনুরূপ বিষয় বর্ণনা করেছেন।
শিয়াগণ এ ঘটনাটিকে ও সাহাবীদের রা. প্রতি কটাক্ষ করার জন্য ব্যবহার করেছেন। তাঁরা বলেনঃ এত বিপুল সংখ্যক সাহাবীর খোতবা এবং নামায ছেড়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও খেল তামাশার দিকে ছুটে যাওয়া প্রমাণ করে, তারা দুনিয়াকে আখেরাতের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতেন। কিন্তু এটি এমন একটি কঠোর অমূলক দোষারোপ যা শুরু বাস্তব থেকে চোখ বন্ধ করেই করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনাটি ঘটেছিল হিজরাতের অব্যবহিত পরে। সে সময় একদিকে সাহাবীদের সামষ্টিক প্রশিক্ষণ ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে অন্যদিকে মক্কার কাফেররা তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি দ্বারা মদীনার অধিবাসীদের কঠোরভাবে অবরোধ করে রেখেছিল যার কারণে মদীনায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দুষ্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছিল। হযরত হাসান বসরী বলেন, সেই সময় মদীনায় মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছিল, কিন্তু জিনিসপত্রের দাম ছিল আকাশ ছোয়া (ইবনে জারীর)। ঠিক এই পরিস্থিতিতে মদীনায় একটি বাণিজ্য কাফেলা এসে হাজির হলে নামাযরত লোকজন এই ভেবে আশঙ্কাবোধ করলো, আমরা নামায শেষ করতে করতে সব জিনিসপত্র বিক্রি না হয়ে যায়। এই ভয়ে তারা সেদিকে ছুটে গিয়েছিল। এটা ছিল এমন একটি ত্রুটি ও দুর্বলতা যা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব ও কঠোর পরিস্থিতির কারণে হঠাৎ করে সেই সময় দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তার পরবর্তী সময়ে এসব সাহাবী ইসলামের জন্য যেসব কুরবানী ও ত্যাগ-তিতিক্ষা দেখিয়েছেন, তা যদি কেউ দেখে এবং ইবাদাত-বন্দেগী ও সামষ্টিক কাজ-কর্মে তাদের জীবন যে অতুলনীয় আল্লাহভীতির সাক্ষ্য দেয় তাও দেখে তাহলে সে একথা বলে তাদের ওপর দোষারোপ করার দুঃসাহস দেখাতে পারবে না যে, তাদের মধ্যে আখেরাতের চেয়ে দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেয়া ব্যাধি ছিল। তবে তার নিজের হৃদয় মনে যদি সাহাবীদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের ব্যাধি থেকে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।
এ ঘটনা সাহাবীদের রা. প্রতি কটাক্ষকারীদের যেমন সমর্থন করে না তেমনি সেসব লোকের ধ্যান-ধারণার প্রতিও সমর্থন জানায় না যারা সাহাবীদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার আতিশয্যে দাবী করেন যে, তাদের দ্বারা কখনো কোন ভুল হয়নি, কিংবা হয়ে থাকলেও কখনো তা উল্লেখ করা উচিত নয়। কারণ তাঁদের ভুল-ত্রুটির উল্লেখ করা এবং তাকে ভুল-ত্রুটি বলা তাদের অপমান করার শামিল। এতে হৃদয় মনে তাদের প্রতি মর্যাদা ও শ্রদ্ধাবোধ অবশিষ্ট থাকে না। তাছাড়া তাদের ভুল-ত্রুটির উল্লেখ সেসব আয়াত ও হাদীসেরও পরিপন্থী যার মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় সাহাবীদের ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়া আল্লাহর নিকট প্রিয় হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এসব কথা স্পষ্ট বাড়াবাড়ি। এর সমর্থনে কুরআন ও হাদীসে কোন দলীল নেই। এখানে যে কেউ দেখতে পারেন, বিপুল সংখ্যক সাহাবীর রা. একটি দল কর্তৃক যে ত্রুটি হয়েছিল আল্লাহ তাআ’লা নিজে এখানে তাদের সেই ত্রুটির উল্লেখ করেছেন। এমন গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত উম্মাতকে পড়তে হবে। সেই গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে গ্রন্থে তাদের ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়া এবং আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার কথাও স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া হাদীস ও তাফসীরের সমস্ত গ্রন্থে সাহাবা কিরাম রা. থেকে পরবর্তীকালের আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের বড় বড় মনীষীগণ পর্যন্ত তাদের এই ত্রুটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ কি এই যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের মন থেকে ঐ সব সাহাবীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে ঐ ত্রুটির উল্লেখ করেছেন যা তিনি নিজেই মানুষের মনে কায়েম করতে চান? অথবা এর অর্থ কি এই যে, এসব অন্ধ ও গোঁড়া ভক্তগণ শরীয়াতের যে মাসয়ালাটি বলে থাকেন সাহাবায়ে কিরাম রা., তাবেয়ীগণ, মুহাদ্দিসগণ এবং মুফাসসিরগণের সে মাসায়ালাটি জানা থাকার কারণে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তারা উল্লেখ করেছেন? আর যারা সূরা জুমআ’ পড়েন এবং তার তাফসীর অধ্যয়ন করেন তাদের মন থেকে কি সত্যি সত্যিই সাহাবা কিরামের রা. প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা উধাও হয়ে গেছে? এ সব প্রশ্নের জবাব যদি নেতিবাচক হয়, আর নেতিবাচক তো অবশ্যই হবে তাহলে সাহাবায়ে কিরামের রা. মর্যাদার নামে কিছু লোক যেসব অনর্থক এবং বাড়াবাড়ি অতিরঞ্জিত ও অতিশয়োক্তিমূলক কথাবার্তা বলে থাকেন তা অবশ্যই ভ্রান্ত।
প্রকৃতপক্ষে সাহাবায়ে কিরাম কোন আসমানী মাখলুক ছিলেন না। বরং এই পৃথিবীতে জন্মলাভকারী মানুষ ছিলেন। তারা যা কিছু হয়েছিলেন তা হয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ সা. এর শিক্ষার গুণে। তাদের এ শিক্ষা দেয়া হয়েছিল ক্রমান্বয়ে বছরের পর বছর ধরে। কুরআন ও হাদীসে আমরা এ শিক্ষার যে নিয়ম-পদ্ধতি দেখতে পাই, তা হচ্ছে যখনই তাদের মধ্যে কোন দুর্বলতা দেখা দিয়েছে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল যথাসময়ে সেদিকে মনোনিবেশ করেছেন এবং দুর্বলতার সেই বিশেষ ক্ষেত্রে অনতিবিলম্বে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদানের একটি কর্মসূচী শুরু করা হয়েছে। জুমআ’র নামাযের এই ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে, বাণিজ্য কাফেলা সংক্রান্ত ঘটনাটি ঘটলে আল্লাহ তাআ’লা সূরা জুমআ’র এ রুকূর আয়াত সমূহ নাযিল করে এ বিষয়ে সতর্ক করলেন এবং জুমআ’র নামাযের নিয়ম-কানুন ও আদব-কায়দা অবহিত করলেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সা. জুমআ’র অনেকগুলো খোতবায় লোকজনের মনে জুমআ’ ফরয হওয়ার গুরুত্ব বদ্ধমূল করে দিলেন এবং বিস্তারিতভাবে তাদেরকে জুমআ’র নিয়ম-কানুন ও আদব-কায়দা শিক্ষা দিলেন। আমরা বিভিন্ন হাদীস থেকে এসব হিদায়াত ও নির্দেশনা স্পষ্টভাবে পেয়ে থাকি। আমরা এ বিষয়ে ১৫ নং টীকায় উল্লেখ করেছি। হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেনঃ জুমআ’র দিন প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য গোসল করা, দাঁত পরিষ্কার করা, যে উত্তম পোশাক তার আছে তা পরিধান করা এবং যদি সম্ভব হয় সুগন্ধি ব্যবহার করা। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী) হযরত সালমান ফারসী বলেন, নবী সা. বলেছেনঃ যে মুসলমান জুমআ’র দিনে গোসল করবে এবং সাধ্যমত নিজেকে বেশী করে পাক পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে, মাথায় তেল দেবে, ঘরে যে খোশবুই থাক না কেন ব্যবহার করবে, তারপর মসজিদে যাবে এবং দুই জন মানুষকে সরিয়ে দিয়ে তাদের মাঝে বসবে না, তারপর আল্লাহর দেয়া সমর্থ অনুসারে নামায (নফল) পড়বে এবং ইমাম যখন খোতবা দিবেন তখন চুপ থাকবে, এক জুমআ’র থেকে পরবর্তী জুমআ’ পর্যন্ত তার কৃত অপরাধসমূহ মাফ হয়ে যায়। (বুখারী, মুসনাদে আহমাদ)। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রা., হযরত আবু হুরাইরা রা. এবং হযরত নুবাইশাতুল হুযালী রা. ও তাদের বর্ণনায় নবী সা. থেকে প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছেন (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, তাবারানী)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, নবী সা. বলেছেনঃ ইমাম যখন খোতবা দেন, তখন যে ব্যক্তি কথা বলে সে গাধার মত যার পিঠে বই পুস্তকের বোঝা চাপানো আছে। আর যে ব্যক্তি তাকে বলেঃ চুপ কর তারও কোন জুমআ’ হয়নি (মুসনাদে আহমাদ) হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। নবী সা. বলেছেনঃ জুমআ’র দিন খোতবার সময় যে ব্যক্তি কথা বলে তাকে যদি তোমরা বলো, “চুপ করো” তাহলে তোমরাও অর্থহীন কাজ করলে (বুখারী মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী, আবু দাউদ)। ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ ও তাবারানী হযরত আলী রা. ও হযরত আবদু দারদা রা. থেকে প্রায় অনুরূপ কিছু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেই সাথে নবী সা. খতীবদেরকেও দীর্ঘ খোতবা দিয়ে মানুষকে বিরক্ত ও অতিষ্ট না করতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি নিজে জুমআ’র দিন সংক্ষিপ্ত খোতবা দিতেন এবং নামাযও খুব দীর্ঘ করে পড়াতেন না। হযরত জাবের রা. ইবনে সামুরা বর্ণনা করেছেন যে, নবী সা. খোতবা দীর্ঘায়িত করতেন না। তাঁর খোতবা হতো কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথার সমষ্টি (আবু দাউদ)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফ বলেনঃ নবী সা. এর খোতবা নামাযের তুলনায় সংক্ষিপ্ত হতো এবং নামায খোতবার চেয়ে দীর্ঘ হতো (নাসায়ী)। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির বর্ণনা করেনঃ নবী সা. বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি নামায দীর্ঘ হওয়া এবং খোতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রমাণ করে সে দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞানের অধিকারী (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম)। বাযযার আবদুল্লাহ ইবনে মাসউ’দ রা. থেকে প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী সা. লোকজনকে কিভাবে জুমআ’র নামাযের নিয়ম-কানুন ও আদব-কায়দা শিখাতেন এসব হাদীসের ভাষ্য থেকে তা অনুমান করা যায়। এভাবে এ নামাযের এমন একটি মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার নজীর পৃথিবীর কোন জাতির সামষ্টিক ইবাদতে দেখা যায় না।
২০. সাহাবীদের যে ত্রুটি হয়েছিল তা কি ধরনের ত্রুটি ছিল এ আয়াতাংশ থেকে তা বুঝা যায় (নাউযুবিল্লাহ)। যদি ঈমানের দুর্বলতা ও জেনে শুনে আখেরাতের ওপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেয়া এর কারণ হতো তাহলে আল্লাহ তাআ’লার ক্রোধ, শাসানি এবং তিরষ্কারের ধরন হতো ভিন্ন। কিন্তু এ ধরনের কোন অপরাধ যেহেতু সেখানে হয়নি বরং, যা হয়েছিল তা প্রশিক্ষনের অভাবে হয়েছিল। তাই প্রথমে শিক্ষকসুলভ ভঙ্গিতে জুমআ’র নিয়ম-কানুন ও আদব-কায়দা শেখানো হয়েছে। তারপর তাদের ত্রুটির কথা উল্লেখ করে মরুব্বিয়ানা ভঙ্গিতে বুঝানো হয়েছে যে, জুমআ’র খোতবা শোনা এবং নামায পড়ার জন্য আল্লাহর নিকট থেকে তোমরা যা লাভ করবে তা এই দুনিয়ার ব্যবসায়-বাণিজ্য ও খেল তামাশার চেয়ে উত্তম।
২১. অর্থাৎ এ পৃথিবীতে রিযিকদানের পরোক্ষ মাধ্যম যে বা যাই হোক না কেন তাদের সবার চেয়ে উত্তম রিযিকদাতা হলেন আল্লাহ তাআ’লা। কুরআন মজীদের বহু সংখ্যকস্থানে এ ধরনের কথা বলা হয়েছে। কোথাও আল্লাহ তাআ’লাকেأَحْسَنُ الْخَالِقِينَ “সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা” কোথাও خَيْرُ الْغَافِرِينَ “সর্বোত্তম ক্ষমাকারী” কোথাও خَيْرُ الْحَاكِمِينَ “সর্বোত্তম বিচারক”, خَيْرُ الرَّاحِمِينَ কোথাও “সর্বোত্তম দয়ালু” এবং কোথাও خَيْرُ النَّاصِرِينَ “সর্বোত্তম সাহায্যকারী” বলা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সৃষ্টি বা মাখলুকের সাথে রিযিক দেয়া, সৃষ্টি করা, দয়া করা এবং সাহায্য করার যে সম্পর্ক তা রূপক বা পরোক্ষ অর্থ প্রয়োগ করা হয়েছে এবং আল্লাহ তাআ’লার ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যারাই তোমাদেরকে বেতন, পারিশ্রমিক বা খাদ্য দিচ্ছে বলে দেখা যায়, যাদেরকেই তাদের শিল্প ও কারিগরী দক্ষতা দিয়ে কিছু তৈরী করতে দেখা যায় অথবা যাদেরকেই অন্যদের অপরাধ ক্ষমা করতে, দয়া করতে এবং সাহায্য করতে দেখা যায় আল্লাহ তাদের সবার চেয়ে বড় রিযিকদাতা, বড় সৃষ্টিকর্তা, বড় দয়ালু, বড় ক্ষমাকারী এবং বড় সাহায্যকারী।
— সমাপ্ত —